
তানিমের এসএসসি পরীক্ষা শেষ। এখন হাতে অফুরন্ত সময়। তার বন্ধুরা সবাই ঘুরতে গেছে। সে-ই কেবল ঘরে বসে ভেরেন্ডা ভাজছে। যদিও তার ধারণা নেই ভেরেন্ডা জিনিসটা আসলে ঠিক কী! নিশ্চয়ই সবজি টাইপের কিছু হবে, যা তেল দিয়ে ভেজে খাওয়া যায়। কে জানে। বিছানায় শুয়ে এই সব হাবিজাবি যখন ভাবছিল, ঠিক সেই সময় মা এসে বললেন, ‘কী রে, তুই দেখি ঘরে বসে থেকে থেকে কুয়ার ব্যাঙ হয়ে যাচ্ছিস। কোথাও থেকে ঘুরেটুরে আয়।’
—কোথায় যাব?
—সেটা আমি কী জানি? তোর যেখানে ভালো লাগে। তবে খুব বেশি দূরে না আবার…
—ছটকু মামার ওখান থেকে ঘুরে আসি?
—হ্যাঁ, তা যেতে পারিস। কাছেই তো আছে, শ্রীমঙ্গল।
‘ওই পাগলা ছোটনের ওখানে গেলে ওর মাথাটা নষ্ট করে দেবে।’ বারান্দায় বসে পেপার পড়ছিলেন বাবা, ফট করে বলে বসলেন। মা-ও রেগে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।
‘ও, আমার ভাই পাগলা, আর তোমার ভাইটা-ই বা কী করছে…?’ মা–বাবার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মাঝখানেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তানিম। ছোট মামার ওখানেই যাবে, মানে ছটকু মামার ওখানে। ছটকু মামা থাকেন সিলেটের শ্রীমঙ্গলে। বাবা ঠিকই বলেছেন। মামাটা একটু পাগলাটে আছে, কিন্তু মজার মানুষ। তাঁর জীবনের একটাই লক্ষ্য, পুরোনো জিনিসপত্র কালেক্ট করা। মানে তিনি একজন অ্যান্টিক কালেক্টর, তাঁর বাড়িটাকে মোটামুটি একটা মিউজিয়ামই বলা যায়। ২৫০ বছরের পুরোনো একটা হাই কমোড আছে তাঁর কাছে। মামার দাবি, এটা নাকি কোনো এক রাজা-বাদশাহ ব্যবহার করতেন। তবে ২৫০ বছর আগে মানুষ হাই কমোড ব্যবহার করত কি না, সেটা নিয়ে তানিমের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে মামার অ্যান্টিক মিউজিয়ামে কিছু কিছু জিনিস আছে, যা সত্যিই ইন্টারেস্টিং। যেমন প্রায় ২০ কেজি ওজনের একটা সিলিং ফ্যান, যা এখনো দিব্যি ঘোরে। কিংবা একটা পিতলের হুক্কা আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। এই হুক্কার কলকেতে আগুন জ্বালাতে হলে মই দিয়ে ওপরে উঠে দাঁড়াতে হয়।
যাহোক, শেষ পর্যন্ত মায়ের কথাই ঠিক হলো। তানিম যাচ্ছে ছোট মামা ওরফে ছটকু মামার বাসায়, শ্রীমঙ্গলে। ঢাকা টু শ্রীমঙ্গল। বাবাই রেলের টিকিট কেটে দিলেন। রাত ১২টায় কমলাপুরে এসে তানিমকে তুলে দিলেন ট্রেনে। বললেন, ‘রেলের বুফেতে গিয়ে কাটলেট খাবি। দারুণ জিনিস। ওটা না খেলে মিস করবি।’
‘আচ্ছা খাব।’ ট্রেনে উঠতে উঠতে বলল তানিম।
‘একা একা ঘুরবি না। ছটকুর সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।’
‘আচ্ছা বাবা আচ্ছা।’ বলল তানিম।
ঠিক সময়েই ট্রেন ছেড়ে দিল। অথচ এই ট্রেন ছাড়ার সময় নিয়ে কত মজার জোকসই না পড়েছে তানিম। একটা জোকস তো এখনো মনে আছে…এক যাত্রী ট্রেনের টিটিকে জিজ্ঞেস করছে ‘পাঁচটার ট্রেনটা কটায় ছাড়বে?’ এই প্রথম তানিম একা একা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে, তা–ও আবার রাতের ট্রেনে। তার বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছে। বাবা বাইরে থেকে চেঁচালেন, ‘আমি ছটকুকে ফোনে বলে দিয়েছি ও স্টেশনে থাকবে।’
‘আচ্ছা।’ জানালা দিয়ে হাত নাড়ে তানিম। আরে বাবা তানিমের নিজের কাছেই তো ফোন আছে, সে যখন–তখন ইচ্ছা করলে মামার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।
ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খিদে পেয়ে গেল তানিমের। বাবা বলে দিয়েছেন, ট্রেনের কাটলেট না খেলে নাকি বিরাট মিস। সে তার ব্যাকপ্যাকটা ওপরের হ্যাঙারে রেখে চলল ট্রেনের শেষ প্রান্তে বুফেতে। বুফেতে ঢুকে একটু অবাক হলো। মাত্র দু–তিনজন মানুষ বসে আছে। যাত্রীদের কারও কি তার মতো খিদে লাগেনি? এর একটা কারণ হতে পারে, সবাই সিটে বসেই খেতে পারে। বুফের অ্যাটেনডেন্টরা নিজেরাই চাহিদামাফিক খাবার নিয়ে এসে হাজির হয়। তানিম একটা কাটলেট আর চায়ের অর্ডার দিল।
মুহূর্তে কাটলেট চলে এল। কাটলেটটা একটু শক্ত টাইপ কিন্তু খেতে বেশ লাগল তানিমের। ট্রেনের দুলুনিতে কাটলেট চিবাতে মন্দ লাগছিল না, অটোমেটিক চিবানো হয়ে যাচ্ছিল যেন। তানিম খেয়াল করল, একটু বুড়োমতো একটা লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে, সাদা পায়জামা–পাঞ্জাবি পরা লোকটাও একটা চা নিয়ে বসে আছে। চোখাচোখি হতেই বুড়োটা হাসল। তানিমও হাসল। একটু পর বুড়ো লোকটা উঠে এসে তার টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসল।
‘তোমার সঙ্গে চা খেতে খেতে একটু গল্প করি। কী বলো?’ তানিম মাথা নাড়ল। যদিও তার একা থাকতেই ভালো লাগছিল।
—নিশ্চয়ই এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে বেড়াতে যাচ্ছ?
—জি।
—এবং মামার বাড়িতে?
তানিম অবাক হলো। লোকটা বুঝল কীভাবে? হা হা করে হাসল লোকটা।
—এটা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে লাগে না। আমরা বাঙালিরা যখন বেড়াতে বের হই, আমাদের প্রথম চয়েস হচ্ছে মামাবাড়ি না হলে দাদাবাড়ি। সেকেন্ড চয়েস কী বলো তো?
—জানি না। মাথা নাড়ে তানিম।
—সেকেন্ড চয়েস হচ্ছে…
লোকটা কথা শেষ না করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়…কী যেন দেখার চেষ্টা করে। ঠিক তখন কেমন একটা মাছের গন্ধ নাকে আসে তানিমের। তবে বুড়ো লোকটা বেশ মজারই। অনেক তথ্য দিল। যেমন সে যে কাটলেট খাচ্ছে, এটা নাকি ব্রিটিশরাই প্রথম চালু করেছিল, যা এখনো চলছে। যদিও আগের সেই মান এখন আর নেই। তবে একটা জিনিস একটু অস্বস্তি লাগল তানিমের; লোকটা চোখের পাতা ফেলে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ঠিক যেন মাছের চোখ।…একটু ভীতিকর!
—আপনি কোথায় যাচ্ছেন? একটা দুটো প্রশ্ন না করলে হয় না। তাই তানিম জানতে চাইল।
—আমি যাচ্ছি মেঘালয়।
—এটা কোথায়?
—ভারতের মেঘালয়।
—কীভাবে যেতে হয়?
—সিলেট গিয়ে তারপর ডাউকি বর্ডার দিয়ে ঢুকব। তুমি তো শ্রীমঙ্গল নামবে তাই না?
এবার তানিম সত্যি সত্যিই অবাক হলো। লোকটা জানল কী করে সে শ্রীমঙ্গল নামবে? তানিমের কেমন যেন একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো! ইচ্ছা ছিল ধীরে ধীরে চা–টা খাবে; কিন্তু সেটা আর হওয়ার নয়। সে দ্রুত চা’টা শেষ করল। চা’টা অবশ্য খুব গরমও ছিল না। চা শেষ করে ‘আচ্ছা আঙ্কেল আসি’ বলে উঠে পড়ল। লোকটা মাছের চোখে তাকিয়ে রইল। তবে মুখের হাসিটা তখনো ঝুলে রইল দুই ঠোঁটের মাঝে।
ভোর পাঁচটা নাগাদ শ্রীমঙ্গল পৌঁছে গেল তানিম। দেখে ঠিক তার ‘ছ’ বগির দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ছটকু মামা।
—কিরে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?
—না।
—গুড, চল। তোর মাকে একটা মেসেজ করে জানিয়ে দে তুই ঠিকঠাকমতো পৌঁছে গেছিস।
—আচ্ছা। তানিম অবশ্য মেসেজ করল না, ফোনই দিল মাকে। ‘মা, পৌঁছে গেছি। এখন ছটকু মামার সঙ্গে যাচ্ছি।’
—সাবধানে থাকিস। একা একা ঘুরিস না, ছটকুর সঙ্গে ঘুরিস।
—আচ্ছা।
—ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করবি।
—আচ্ছা, আচ্ছা।
তিন চাকার একটা অদ্ভুত মোটরগাড়িতে উঠে ওরা রওনা দিল। গাড়িতে ওঠার সময় দেখে, টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বুড়ো লোকটা। লোকটা না বলল সে সিলেট যাচ্ছে, তারপর ভারতের মেঘালয় যাবে? তাহলে শ্রীমঙ্গলে নামল কেন! শিরশিরে অনুভূতিটা আবার হলো তানিমের, যেন একটা ঠান্ডা বাতাস ছুঁয়ে গেল তাকে।
ছটকু মামার বাসাটা সত্যি দারুণ। প্রতি এক ইঞ্চি পরপর প্রাচীন সব জিনিসে ভরা। বহু আগে, তানিম যখন সিক্সে পড়ত, তখন একবার মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল, তখনো এত জিনিস ছিল না। এখন মনে হচ্ছে অ্যান্টিক জিনিসপত্র আরও বেড়েছে। সবচেয়ে অবাক হলো ফ্রিজটা দেখে। ঘরের প্রায় মাঝখানে একটা বিশাল ফ্রিজ!
—মামা, তুমি না ফ্রিজ একবারেই পছন্দ করো না?
—হ্যাঁ, করি না তো। আমি বাসি খাবার একদম খেতে পারি না। তাই ফ্রিজ পছন্দ করি না।
—তাহলো এটা? এটা তাহলে অ্যান্টিক ফ্রিজ?
—না, এটা সত্যি ফ্রিজ। তবে প্রায় অ্যান্টিক। জানিস তো আমি আবার ঠান্ডা পানি ছাড়া খেতে পরি না। তাই এই ফ্রিজটা কিনলাম, সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ। দাম খুবই কম। তবে এই ফ্রিজের একটা ইতিহাস আছে
—কী ইতিহাস?
—রাতে বলব। এখন যা হাত–মুখ ধুয়ে আয়। চাইলে গোসলও করতে পারিস। গিজারে গরম পানি আছে। আমি তোর জন্য নাশতা রেডি করি। মামার বাসায় কোনো কাজের লোক নেই। সবকিছু তিনি দশ হাতে একাই করেন।
গোসল করে ফেলল তানিম। গিজারের হালকা গরম পানিতে গোসল করতে মন্দ লাগল না। গোসল করে নতুন এক সেট জামাকাপড় পরে বের হয়ে এল নিজের রুম থেকে। ফ্রিজটা যেখানে আছে তার ঠিক পাশের রুমটা তানিমের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, আরেক পাশে মামার রুম। বাড়িটা পুরোনো কিন্তু অনেকগুলো রুম এবং প্রতিটা রুমে যথারীতি প্রাচীন সব জিনিস। যেমন তানিমের রুমেই আছে প্রায় ১০–১২টি প্রাচীন জিনিস, ছোট ছোট টুলের ওপর সাজানো। একটা কেটলি টাইপের জিনিস, যেটাকে মামা বললেন রাশিয়ান সামোভার আর আছে একটা গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক, যদিও নষ্ট। মামা অবশ্য বলেন, একটা নষ্ট ঘড়িও দিনে দুবার সঠিক সময় দেয়…।
—কিরে তোর হলো? মামা চেঁচান। ডাইনিংয়ে চলে আয় জলদি।
—এই আসছি।
ডাইনিং টেবিলে এসে তানিমের মাথা নষ্ট হওয়ার জোগাড়। কী নেই! পরোটাভাজি ডিম তো আছেই, আছে ফ্রেঞ্চফ্রাই, কেক, আরও আছে কুমিল্লার প্যাড়া, টাঙ্গাইলের চমচম…আর নেত্রকোনার বিশাল সাইজ বালিশ মিষ্টি। সেই সঙ্গে নানা জাতের আম।
—এত কিছু কোথা থেকে আনলে মামা?
—আরে তুই একমাত্র ভাগনে, তোর জন্য না আনলে কার জন্য আনব। তুই তো মিষ্টি পছন্দ করিস।
—তা করি, তাই বলে এত মিষ্টি?
যাহোক, খেতে খেতে নানা গল্প হলো। মামা জানালেন তিনি খুব শিগগির একটা ‘কগনিটিভ রেভল্যুশন’ যুগের পাথরের তৈরি অস্ত্র পেতে যাচ্ছেন।
—কগনিটিভ রেভল্যুশনট কী?
—এটাকে বাংলায় বলা যায় বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব।
—বুঝলাম না।
—ধর, প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে মানুষ আর প্রাণীদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে হোমোসেপিয়েন্সদের মধ্যে একটা কগনিটিভ রেভল্যুশন হলো। মানে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ঘটল ওদের মাথায়। আচ্ছা বাদ দে এখন। এটা নিয়ে পরে বলব তোকে। এখন বালিশ মিষ্টিটা খা।
ছটকু মামা মাঝেমধ্যে এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলে যে তানিমের মাথার ওপর দিয়ে যায়।
—এত বড়টা খেতে পারব না।
—যতটুক পারিস খা।
এখানে বলে নেওয়া ভালো, ছটকু মামা বিয়ে করেননি। কাজেইু তানিমের কোনো মামি নেই। মামার যুক্তি হচ্ছে, এই যে আমার অ্যান্টিক কালেকশন যদি আমার বউ আই মিন তোর মামি পছন্দ না করে, তখন লাগবে ভেজাল। আমি আমার এই সব প্রাচীন জিনিস ছাড়া থাকতেই পারব না।
যাহোক, নাশতা শেষ করে, শ্রীমঙ্গলের বিখ্যাত চা খেয়ে মামার সঙ্গে ঘুরতে বের হলো তানিম। সেই অদ্ভুত গাড়িতে করে প্রথমে গেল একটা ঝাউবনে, জায়গাটার নাম হরিণছড়া। পাহাড়ের ওপর বিশাল বিশাল আকাশছোঁয়া ঝাউগাছ। সত্যি অসাধারণ জায়গা। তারপর দেখল বিশাল প্রান্তরজুড়ে ফিনলের চা–বাগান, শুধু ফিনলে নয়, আরও অনেক অনেক বড় কোম্পানির চা–বাগান। সেই সব বাগান থেকে নারীরা চা–পাতা সংগ্রহ করছেন। তারপর মাথায় মস্ত একটা ঝুড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছেন চা–পাতা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল ২১ কেজি পাতা তুললে তাঁরা পান ১৭০ টাকা। আগে পেতেন ১৪০ টাকা, তাঁরা আন্দোলন করে ৩০ টাকা বাড়িয়েছেন। মামার কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেল, যেমন কাঁচা কচি চা–পাতার ওজন অনেক বেশি, আর ‘নিশিগাছ’ নামে একটা গাছ আছে, এই গাছ যেখানে থাকে, সেখানেই চা–বাগান হয় বা চা–বাগান করা যায়।
ফেরার পথে পথের ধারের একটা রেস্টুরেন্টে মজার শিঙাড়া খেলো। আর খেলো সাত লেয়ারের চা। জিনিসটা মোটেও সুখকর মনে হলো না তানিমের কাছে। যাহোক, বাইরে খেয়েদেয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকেল চারটা। গিজারের গরম পানিতে ফের গোসল করে ঘুম দিল। এক ঘুমে বিকেল পার।
রাতে খাবার টেবিলে আরেক চমক। রুমালি রুটি আর গরুর চাপ। রুমালি রুটির সাইজও সে রকম, রাতে কাঁথা হিসেবে দিব্যি গায়ে দিয়ে ঘুমানো যাবে…এতই বড় সাইজ। আরও ছিল পরোটা আর বেগুনভাজি। আরাম করে খেল তানিম। এত কিছু মামা বানায় না। তার পরিচিত এক লোক আছে, সে নিয়মিত সাপ্লাই দেয়। খাওয়ার মধ্যেই তানিম জানতে চাইল—
মামা ফ্রিজের গল্পটা বললে না?
ও হ্যাঁ, বলব বলব, ভয় পাবি না তো?
না । কেন ভয়ের কিছু আছে নাকি?
থাকতেও পারে। আচ্ছা, আগে বল তো, এই বিশাল ফ্রিজটার দাম কত?
কত?
আহা, আন্দাজ করো না।
২০ হাজার?
হা হা…মাত্র ৩ হাজার।
কী বলো?
হ্যাঁ… তাহলে শোন কেন কম দাম।
বলো।
এই ফ্রিজটার বয়স ধর মিনিমাম ৪০-৫০ বছর হবে, ৬০-ও হতে পারে। পুরোনো ফ্রিজ বুঝতেই পারছিস। খেয়াল করেছিস, এই ফ্রিজের লক সিস্টেম আছে। মানে বাইরে থেকে তালা মারা যায়।
কিন্তু মামা, তোমার ফ্রিজে পানি ছাড়া তো কিছু নেই। তালা মারার দরকারও নেই।
হ্যাঁ তা নেই…তাহলে শোন মূল গল্পটা।
মামা কেশে গলা পরিষ্কার করে গল্প শুরু করলেন।
অবশ্য গল্প না এটা, সত্যি কাহিনি। এই ফ্রিজটা যাদের ছিল, তারা যথেষ্ট ধনী ছিল। তাদের কোনো ছেলে বা মেয়ে ছিল না। তবে স্বামী লোকটা ছিল বদ টাইপের। সে নাকি তার স্ত্রীকে অত্যাচার করত বলে শোনা যায়। তো একদিন স্ত্রী প্রতিশোধ নিল। স্বামীকে খাবারের সঙ্গে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল।
বলো কী?
এখানেই শেষ না। স্ত্রী স্বামীর বডিটাকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে লক করে চাবি ফেলে দিল।
কোথায় ফেলে দিল?
এমন কোথাও ফেলল যেন আর চাবি খুঁজে না পাওয়া যায়।
তারপর?
তারপর ওই অবস্থায় বাড়ির সবকিছু বিক্রি করা শুরু করল, ফ্রিজটাও ওই রকম বন্ধ অবস্থায় পানির দরে বিক্রি করে মহিলা উধাও হয়ে গেলেন। তাকে আর কেউ কখনো দেখেনি কোথাও!
তারপর?
তারপর আর কী, যে ফ্রিজটা কিনল, সে টের পেল তার ফ্রিজ থেকে পচা গন্ধ বের হচ্ছে। তখন ফ্রিজ ভেঙে দেখে মানুষের লাশ। ব্যস, তারপর তো হইচই। কত কাহিনি…
শেষ পর্যন্ত এই ভয়ংকর জিনিসটা তোমার কাছে এল কী করে?
আমি আসলে সস্তায় একটা ফ্রিজ খুঁজছিলাম। কীভাবে কীভাবে এই ফ্রিজটার খোঁজ পেলাম। এই ফ্রিজের পেছনের কাহিনি শুনে কেউ কেনে না বলে ফ্রিজটা পড়েই রইল একটা গোডাউনে বহুদিন। তারপর আর কী, একসময় আমি মাত্র তিন হাজার টাকায় কিনে ফেললাম। হা হা হা।
কিন্তু তোমার রাতে ভয় করে না?
ভয় করবে কেন? ফ্রিজের ভেতরে কি ওই বদ হাজব্যান্ডটা এখনো বসে আছে মনে করিস তুই?
তা নেই কিন্তু…
কেনার পর টানা এক মাস আমি ফ্রিজটা ধুয়েছি, সার্ফ এক্সেল, হুইল পাউডার, হারপিক যত রকম সাবান আছে, সব দিয়ে ধুয়েছি। তারপর ব্যবহার করা শুরু করেছি।
ফ্রিজটা তাহলে ঠিক ছিল?
হ্যাঁ কেনার পর এর পেছনে আমার ধোয়াধুয়ি ছাড়া কোনো খরচ করতে হয়নি। একদম ঠিক ছিল।
তারপর আরও অনেক গল্প হলো। ফাঁকে ফাঁকে আম খাওয়া হলো। তানিমের প্রিয় আম্রপালি আম। তবে মামা আরেক পদের আম খাওয়ালেন, সেটা হচ্ছে গৌড়মতি আম। অসাধারণ মিষ্টি। হলুদের ওপর বুটি বুটি আমটার মিষ্টির ধরনটাই অন্য রকম। মামা বললেন, ‘আরে আমের সিজন এখন শেষ, তোর আম্রপালি আম তো দূরে থাক, গাছও খুঁজে পাবি না কদিন পর। এখন কিছুদিন পাবি এই গৌড়মতি আম।’ আমটা সত্যি অসাধারণ।
রাতে শুতে গিয়ে বেশ ভয় ভয় করতে লাগল তানিমের। তার ঘর থেকে বের হলেই ফ্রিজটা দেখা যায়। মামা কেন যে গল্পটা বলল। মামা অবশ্য বলেছে তোর ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছে হলে ফ্রিজ থেকে পানি খাস। তবে তোর ঘরের টেবিলের ওপরই পানির বোতল আছে। আর ঠান্ডা খেতে চাইলে ফ্রিজে বোতল আছে।
তানিম বাসা থেকে একটা বই এনেছিল। বইটা অবশ্য বেশ হাসির। লেখক শিবরাম চক্রবর্তী, তার প্রিয় লেখক। ‘হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন’ গল্পটা পড়তে শুরু করল তানিম। কিন্তু কেন যেন মোটেও হাসি আসছিল না। কেমন একটা ভয় ভয় ভাব ভেতরে থেকেই যাচ্ছে। মাথা থেকে ফ্রিজের ওই গল্পটা যাচ্ছেই না। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, ফ্রিজের পাশের ঘরটাই মামার ঘর। অর্থাৎ ফ্রিজের একদিকে ছটকু মামা আরেক দিকে তানিম।
কয়টা পর্যন্ত তানিম শিবরামের বই পড়েছে, সেটা তানিমও জানে না। একসময় চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তানিমের। বই রেখে উঠে বসল, ঘুমানোর আগে এক গ্লাস পানি খাওয়া তানিমের অনেক দিনের অভ্যাস। বাসায় থাকলে মা বিছানার পাশের টেবিলে গ্লাস ভরে ঠান্ডা পানি রেখে দিতেন। এখানেও মামা পাশের টেবিলে বোতলে পানি ভরে রেখেছেন। কিন্তু পানিটা বেশ গরম, ছটকু মামার মতোই ঠান্ডা পানি খাওয়া তানিমের অভ্যাস। কাজেই গুটি গুটি পায়ে তানিম এসে ফ্রিজের সামনে দাঁড়াল। তখনই আবার ফ্রিজের গল্পটা মাথায় চলে এল। কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো তার।
ফ্রিজের দরজায় হাত দিতে যাবে, তখনই কট করে একটা শব্দ হলো। পুরোনো ফ্রিজ কত রকম শব্দ হতেই পারে। কট করে শব্দটা আবার হলো। শব্দটা ফ্রিজের ভেতর থেকেই আসছে সন্দেহ নেই…আর তখনই আস্তে করে ফ্রিজের দরজাটা খুলে গেল নিজে নিজে, যেন কেউ ভেতর থেকে দরজাটা খুলে দিয়েছে। তানিম লাফিয়ে সরে আসতে গিয়েও পারল না। মনে হলো, তার পা জোড়া কে যেন মেঝের সঙ্গে সুপার গ্লু দিয়ে আটকে দিয়েছে। অসম্ভব ভারী লাগছে পা দুটো। তানিমের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই…ঠিক তখনই তানিম বিস্ফারিত চোখে দেখল ধবধবে সাদা একটা পা ফ্রিজের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে…প্রচণ্ড আতঙ্কে একটা আর্তচিত্কার দিল তানিম। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোল না। কেমন একটা ঘর্ঘর আওয়াজ হলো…তানিম টের পেল, আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছে সে…পড়ে যাচ্ছে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে সে পেছন দিকে পড়ে যাচ্ছে…আর সেই ধবধবে সাদা পা-টা তখনো ফ্রিজের ভেতর থেকে নামছে… নামছে… নেমে আসছে!
তানিমের যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখে তার মাথার ওপর ঝুঁকে আছে ছটকু মামা। তানিমের মাথা ভেজা। পানিতে জবজব করছে।
কিরে তানিম, ভয় পেয়েছিলি?
তানিম মাথা নাড়ে। মামা তখন একটা কাণ্ড করলেন। এক হাতে একটা সাদা পা দেখালেন। ‘এটা দেখে ভয় পেয়েছিস তাই না? গাধা, এটা পোরসিলিনের একটা নকল পা। ফ্রিজে রেখেছিলাম কারণ, জিনিসটা ডেলিভারি দিয়েছে যে গাড়িতে করে, সেটার ডিকিতে সমস্যা ছিল, আগুনের মতো গরম হয়েছিল ডিকিটা, পা-টাও গরম হয়েছিল। তাই ভেবেছিলাম, একটুক্ষণ ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করি। কিন্তু বের করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আর তুই রাতে পানি খেতে এসে ভয় পেয়েছিস। হি… হি…’। মামার হাসিটা মজার। বাচ্চাদের মতো। মামার কাণ্ডকারখানাই সব অদ্ভুত। পোরসিলিনের পা-টা ফ্রিজে রাখার দরকার কী ছিল? বাইরে থাকলে আপনা-আপনি কি ঠান্ডা হতো না?
আমার মাথা ভেজা…
ওহ, তোর জ্ঞান ফেরাতে একটা পানির ঝাপটা দিয়েছি, তাতেই…ওঠ, উঠে বস। তোকে এই ভয় পাওয়া পায়ের ইতিহাসটা বলি। এটা খুবই অ্যান্টিক জিনিস। অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি।
তানিম উঠে বসল। এখন পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে বেশ হাসি পাচ্ছে। সামান্য একটা ব্যাপার আর সে কিনা ভেবেছিল ফ্রিজের ভেতর থেকে সেই লোকটা ভূত হয়ে নেমে আসছে।
মামা চমত্কার কফি বানায়। যদিও তানিম কফি বা চা খেতে তেমন পছন্দ করে না। তবে খাবার টেবিলে বসে গরম কফি খেতে এখন বেশ ভালো লাগছে। মামাও কফি নিয়ে বসেছে। কিছুক্ষণ কফি নিয়ে বক্তৃতা করলেন তারপর শুরু করলেন নকল পোরসিলিনের পায়ের কাহিনি।
এই পা-টা হচ্ছে রাজা শ্রী হরিশ্চন্দ্রের নকল পা। উনি ওডিশার শেষ রাজা ছিলেন। তার একটা পা ছিল না। কিন্তু সেটা কেউ জানত না। তার মৃত্যুর পর সেটা সবাই জানতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই পা পরে নিলামে ওঠে। আরেক রাজা কিনে নেয় চড়া দামে। তারপর সেই রাজার কোষাগার থেকে সেটা চুরি হয়ে যায়। তারপর বহু হাত ঘুরে… না না ভুল বললাম বহু পা ঘুরে… হা হা হা।
মানে বুঝলাম না, হাসছ যে?
হাসলাম, কারণ এই নকল পা-টা আরও অনেকে ব্যবহার করেছে। নকল পা হিসেবেই, এই জন্যই বললাম বহু পা ঘুরে…তবে শেষ পর্যন্ত এটা একটা ‘লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড’ টাইপ প্রতিষ্ঠানে পড়ে ছিল দীর্ঘদিন। তারপর আরও কয়েক হাত ঘুরে এটা এখন আমার জিম্মায়।
তানিম ধবধবে সাদা পা–টার দিকে তাকায়; জিনিসটা এখন টেবিলের ওপর দিব্যি শোভা পাচ্ছে। কী ভয়টাই না পেয়েছিল তানিম। ভয় পাওয়ারই কথা।
বাকি রাতটা আরামেই ঘুমাল তানিম। একটা সুন্দর স্বপ্নও দেখে ফেলল… যেন সে চা–বাগানের মহিলাদের সঙ্গে চা–পাতা তুলছে। চা–বাগানের মহিলারা বলছে, ‘একি তুমি দেখছি সব পাতা তুলে ফেলছ, তাহলে আমরা তুলব কী?’
‘সব পাতা আপনাদের জন্যই তুলছি। দেখছেন না, আমার হাত দুটো সত্যি হাত না, আসলে মেশিন। মেশিনের হাত দিয়ে কী দ্রুত তুলছি।’ দেখতে দেখতে পুরো চা–বাগানের সব পাতা সে তুলে ফেলল একাই। তারপর চেঁচিয়ে বলল, ‘এবার আপনারা এগুলো নিয়ে নিন…’ মহিলারা সবাই খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবুজ কচি চা–পাতা তাদের ঝুড়িতে ভরতে লাগল। তখনই ঘুমটা ভাঙল। বেলা তখন ১১টা। উঠে দেখে তার হাত দুটো টনটন করছে, রাতজুড়ে চা–পাতা তোলার জন্য! আসলে বেকায়দায় শোয়ার জন্য হাত দুটো ব্যথা করছে আর সে কিনা স্বপ্ন দেখল চা–পাতা তুলছে তার মেশিনের হাত দিয়ে।
কেন মামা?
কারণ হচ্ছে ‘ই য়াক! ই য়াক!!’ (Yi aakh! Yi aakh!) অর্থ আকাশে ইগল দেখা গেছে, সাবধান!! তখন তারা সাবধানতার জন্য নিচে নেমে পড়ে
আর ‘কে য়াক! কে য়াক?’
আর ‘কে য়াক! কে য়াক!!’ (k yak! k yak!!) অর্থ মাটিতে সিংহ বা বাঘ দেখা গেছে, সাবধান!! তারা তখন লাফিয়ে গাছে উঠে পড়ে। ব্যাপারটা মজার না?
অনেক মজার।
মামার কাছ থেকে এ রকম খুচরা জ্ঞান অর্জন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেল তানিম। খাসিয়াপাড়া নামে ছোট্ট একটা পরিচ্ছন্ন আদিবাসীদের কমিউনিটি ঘুরে বাসায় ফেরার পথ ধরল। বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা।
সে রাতে খাওয়া হলো তন্দুর রুটি আর গরুর মাংস। বেশ লাগল। খাওয়াদাওয়ায় মামা বেশ শৌখিন, বেশির ভাগ তিনি নিজেই তৈরি করেন, বাকি কিছু আইটেম বাইরে থেকে আসে। রান্নাবান্নার তার কিছু অ্যান্টিক তৈজসপত্রও আছে। সবশেষে মামার সেই অসাধারণ কফি। প্রথম দিকে তানিমের কেমন কাঠপোড়া কাঠপোড়া একটা গন্ধ লাগত, এখন আর তা লাগছে না। মনে হচ্ছে ঢাকায় গিয়ে তাকে কফি ধরে ফেলতে হবে। খুব টায়ার্ড লাগছিল বলে আজ আর বই পড়া হলো না। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম।
কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তানিম জানে না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা ফরফর শব্দে। আজ সে লাইট জ্বালিয়েই ঘুমিয়েছে। দেখে শব্দটা একটা পলিথিনের। একটা সাদা বেশ বড় পলিথিন ফ্যানের বাতাসে ঘরের চারদিকে গোল হয়ে উড়ছে। তারই ফরফর শব্দ। শব্দটা এই মধ্যরাতে বেশ ভীতিকর। একসময় পলিথিনটা ফ্যানের ব্লেডে জড়িয়ে গেল। তখন শব্দটা আরও বিশ্রীভাবে হতে লাগল। তানিম উঠে গিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করল। ঘরের কোনায় একটা ছাতা ছিল। বিছানায় দাঁড়িয়ে সেটা দিয়ে পলিথিনটা নামিয়ে আনল। তারপর কোনার ঝুড়িতে ঢুকিয়ে রাখল পলিথিনটাকে। ওটা আসলে বেশ বড় সাইজের সাদা রঙের ছেঁড়া পলিথিন, ঘরের ভেতর কী করে এল কে জানে। নিশ্চয়ই আসে পাশেই ছিল ফ্যানের বাতাসে উঠে এসেছে।
তানিম ভাবল, পানি খাওয়া যাক। আজ আর তেমন ভয় করল না। ঘর থেকে বাইরে এসে দেখে, ফ্রিজের সামনে মামা। মামাও কি পানি খেতে বের হয়েছেন? তখনই বুকটা ধক করে উঠল। ওটা মামা নন। অতি অবশ্যই মামা নন। এই বাসায় সে আর মামা ছাড়া কেউ নেই। এটা তৃতীয় কেউ। পেছন ফিরে লোকটা কিছু করছে ফ্রিজের দরজা খুলে। হঠাৎ লোকটা ঘুরে তাকাল তানিমের দিকে। তানিমের মনে হলো, সময় যেন থেমে গেছে। তার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে আটকে গেছে, ধক ধক করছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! লোকটা আর কেউ নয়, সেই ট্রেনের বুড়ো লোকটা। তার গায়ে সাদা একটা পলিথিন জড়ানো, বর্ষাতির মতো করে জড়িয়ে রেখেছে শরীরে, যেন এখনই বৃষ্টি পড়বে, তাই সাবধানতা। লোকটা তানিমের দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন হাসল। যেন বলছে, ‘কি, চিনতে পারছ না? আমি সেই লোক…যার চোখের পলক পড়ে না, সব সময় মাছের মতো তাকিয়ে থাকতে পারে।’ মানুষ যখন প্রচণ্ড ভয় পায়, তখন শরীরে অ্যাড্রেনাল হরমোনের নিঃসরণ হয়। ‘ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট’ অবস্থা তৈরি হয়। হৃৎপিণ্ড অতিরিক্ত রক্ত পাম্প করে দ্রুত শরীরের প্রতিটি পেশিতে পাঠানোর চেষ্টা করে, যেন ভয়ের বিষয়টাকে মোকাবিলা করবে, নইলে ভয়ের জায়গা থেকে পালিয়ে যাবে। ছুটে পালিয়ে যেতেও শক্তির প্রয়োজন হয় বটে। জীববিজ্ঞান ক্লাসে আকবর স্যার বিষয়টা তাদের সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন, তানিমের মনে আছে। তানিম বেশ বুঝতে পারছে যে সে এখন ‘ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট’ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তার শরীরে নিশ্চয়ই অ্যাড্রেনাল হরমোনের নিঃসরণ হচ্ছে। সে চিত্কার করে উঠল। চিৎকারে কী যে বলল, তা সে নিজেও জানে না। সে যখন চিত্কার করে উঠল, তখন নিশ্চয়ই তার চোখ দুটো কয়েক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয়েছিল। চোখ খুলতেই তানিম দেখল, সেখানে সাদা পায়জামা–পাঞ্জাবি পরা বুড়ো লোকটা নেই। ফ্রিজের দরজাটা খোলা। সেখানে লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছে ছটকু মামা। মামার দুচোখে বিস্ময়। ‘আমার নিশ্চয়ই হ্যালুসিনেশন হয়েছে,’ বিড়বিড় করে বলল তানিম।
—কিরে, আবার ভয় পেয়েছিস নাকি?
—ন-না না!
—কে যেন চেঁচাল মনে হলো!
—না তো। পানি খেতে এসেছিলাম।
—ও, তা–ই বল! বাইরে অবশ্য নাইটগার্ডরা কী সব যেন বলে চেঁচায়। এই নে পানি।
মামা একটা ঠান্ডা পানির একটা বোতল এগিয়ে দিল।
—কফি খাবি নাকি এক কাপ?
—না না, তুমি খাও।
—মাঝরাতে এক কাপ কফি না খেলে আবার আমার হয় না।
মামা কফি বানানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। তানিম পানির বোতলটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। কেন যেন বিষয়টা মামাকে বলতে ইচ্ছা করছে না। এক নিশ্বাসে পানির বোতলটা খালি করে ফেলল তানিম। তখনই তার নজর পড়ল, ঘরের কোনায় প্লাস্টিকের ঝুড়িটার ওপর। যেখানে পলিথিনটা থাকার কথা, সেখানে সেটা নেই। অথচ তানিমের স্পষ্ট মনে আছে, সে নিজের হাতে পলিথিনটা ভাঁজ করে ঝুড়ির ভেতর ঢুকিয়েছিল, যেন আবার ফ্যানের বাতাসে উড়ে না যায়।
বাকি রাত আর তানিম ঘুমাতে পারল না। জেগে রইল। শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির বইটার একটা গল্প পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা পাতাও এগোতে পারল না। কোনোমতে রাতটা পার করল সে।
পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে তানিম বলল, আচ্ছা মামা, ওই লোকটার বয়স কেমন ছিল?
—কোন লোক?
—এই যে তোমার ফ্রিজের ভেতর যে লাশটা ছিল!
—উফ! তোর মাথা থেকে এটা যাচ্ছে না, না?
—না এমনি একটু কৌতূহল!
—শুনেছি লোকটা বয়স্ক ছিল, ৬০–৬৫ হবে! ফ্রিজের ভেতর একটা বড় পলিথিনে প্যাঁচানো ছিল লাশটা। লোকটার চোখ দুটো নাকি খোলা ছিল, যেন তাকিয়ে আছে, মাছের চোখের মতো নিষ্পলক। অবশ্য এসবই শোনা কথা। বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আবার কে জানে, সত্যিও হতে পারে!
—মামা..
—বল।
—আমি আজই চলে যাব।
—কী বলছিস! এলি তো মাত্র দুদিন। ভয় পেয়েছিস নাকি?
—না না, ভয় না।
—তাহলে?
ঠিক তখন বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। কে যেন এসেছে। দেখা গেল, মামার ছোটবেলার বন্ধু রবিন। দুই বন্ধু পরস্পরকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে রীতিমতো হাউকাউ শুরু করে দিলেন।
—এত দিন কোথায় ছিলি?
—আমি তো এখানেই আছি। তুই কোথায় ছিলি, সেটা বল।
—আমি যেখানে থাকার সেখানেই ছিলাম।
—তারপর… আছিস কেমন? দেশে আছিস না বিদেশে?
—দুই জায়গায়ই আছি। এ কে?
—চিনতে পারিসনি? ছোটবেলায় দেখেছিস, আমার বড় বোন রেণু বুবুর ছেলে। ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছে।
—ও! মনে পড়েছে। তানিম না? এত বড় হয়ে গেছে বাব্বা! কেমন আছ তানিম? চিনতে পেরেছ?
তানিম অবশ্য চিনতে পারল না। তবে মামার যে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তা বেশ বোঝা গেল। দুই বন্ধুর প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর আবার নতুন করে চা–নাশতা চলে এল টেবিলে। আরেক দফা খেতে হল তানিমকেও। রবিন মামা দারুণ এক মিষ্টি নিয়ে এসেছেন, সেটাও খেতে হলো। আড্ডায় আড্ডায় তানিমের ঢাকায় ফেরার ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল।
একসময় রবিন মামা উঠে পড়লেন, তাঁকে ঢাকায় ফিরতে হবে। ঢাকায় জরুরি কিছু কাজ আছে। সেসব কাজ সেরে রাতের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুরের দিকে ছুটতে হবে।
—সেকি রে! আজকের দিনটা অন্তত থাক। তোর আসা উপলক্ষে ভালোমন্দ কিছু খাই। আমার ভাগনেটাও পালাই পালাই করছে। তুই থাকলে বেশ হয়।
—কী? ভাগনে চলে যাবে? তাহলে আমার সঙ্গে চলুক।
—না না, ও আরও কটা দিন থাক।
—না মামা, চলে যাই।
—বুঝতে পেরেছি, তুই আসলে ভয় পেয়েছিস।
—ন-না না।
—সত্যি যাবি? তাহলে রবিনের সঙ্গেই নাহয় চলে যা, ওর গাড়িতে। রবিন, তুই নতুন গাড়ি কিনেছিস মনে হয়! আগেরটা তো এমন ছিল না।
—আগেরটার অবস্থা আর বলিস না। ওটার হর্ন ছাড়া আর সবই বাজত। হা হা…তোর জাদুঘরে রাখার মতো অবস্থা আরকি!
দুই মামা নিজেদের রসিকতায় হো হো করে হাসতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে এতই ফুর্তি যে সামান্য কিছুতেই হো হো করে হাসছিলেন। আর হাসি যেহেতু ছোঁয়াচে, তাই তানিমও হাসছিল। রাতের সেই ঘটনা ভুলে থাকার জন্য এখন হাসিটাই যেন খুব বেশি দরকার।
শেষ পর্যন্ত তানিম রবিন মামার সঙ্গে রওনা দিল ঢাকার উদ্দেশে। যাওয়ার সময় ছটকু মামা ৫০০ টাকার একটা কচকচে নোট তানিমের বুকপকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। রবিন মামাই গাড়ি চালাচ্ছেন। পথে টুকটাক আলাপ হলো দুজনের। রবিন মামা জানতে চাইলেন, তানিমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। রেজাল্ট বের হলে পর তানিম কোন কলেজে ভর্তি হবে ইত্যাদি। এসব গল্প করতে করতে একসময় হঠাৎ রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করালেন রবিন মামা।
—কী হলো মামা?
—চাকায় কেমন একটা শব্দ হচ্ছে।
মামা নেমে গেলেন। তানিমও নামল। দেখা গেল, পেছনের চাকায় একটা সাদা পলিথিন বিশ্রীভাবে পেঁচিয়ে আছে…সেই পলিথিনটা? তানিমের ভেতরটা কেঁপে উঠল। এসব কী হচ্ছে? আবার সেই পলিথিন!
—কোনো মানে আছে? এই পলিথিন কোত্থেকে এসে চাকায় আটকাল?
বিরক্তিতে চুল খামচে ধরলেন রবিন মামা। অনেকটা সময় নিয়ে ঝামেলা করে পলিথিনটা সরানো গেল চাকা থেকে। তানিমের ইচ্ছা হলো, পুরো ঘটনাটা রবিন মামাকে বলতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না।
বাকি রাস্তা নির্ঝঞ্জাট গাড়ি চলল। খুব একটা যানজটেও পড়তে হলো না। সন্ধ্যার দিকে তানিম বাসায় পৌঁছাল। রবিন মামা তানিমকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেলেন। বাসায় ঢুকলেন না। তাঁর হাতে একদম সময় নেই। তানিমকে দেখে মা ভীষণ অবাক হলেন!
—কী রে, এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে! শ্রীমঙ্গল ভালো লাগেনি?
—লেগেছে, অনেক সুন্দর।
—তাহলে চলে এলি যে!
—মামার এক বন্ধুর গাড়িতে চলে এলাম। তুমি চিনবে হয়তো, রবিন মামা।
—ও, রবিন! ও বাসায় এল না?
—না, ওনার অনেক কাজ। সময় নেই। সিঙ্গাপুরে যাবেন বললেন।
—তা এসে তুই ভালোই করেছিস। কাল রাতে একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছি তোকে নিয়ে। ছটকু ভালো আছে তো?
—হুম। কী স্বপ্ন মা?
—থাক, শুনে কাজ নেই। যা চট করে গোসল করে নে। আমি টেবিলে ভাত দিই। ক্ষুধা লেগেছে নিশ্চয়ই?
—তা লেগেছে।
অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল তানিম, পুরো ঘটনাটা কি কাউকে বলবে? ভাবতে লাগল। না, বলবে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিছু কিছু রহস্য নিজের কাছেই থাক বরং।
গল্পটা এখানে শেষ হয়ে গেলেই হয়তো ভালো হতো। কিন্তু আরেক দিন আরেকটা ঘটনা ঘটল। আরেফিনদের বাসা থেকে ফিরছিল তানিম, আরেফিন তার সহপাঠী। সন্ধ্যা হয়ে আসছে প্রায়, হঠাৎ বাসার কাছের একটা টং দোকানে দেখল সেই লোকটাকে। সেই বুড়ো হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার দুই হাতে দুই কাপ চা। তানিম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, শরীরে একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো তার। তখনই লোকটা চাসহ এক হাত তুলে ডাকল তাকে, ভাবটা এমন, এসে চা খেয়ে যাও…। তানিম অবশ্য লোকটার ডাকে সাড়া দিল না। তার প্রচণ্ড ভয় হলো। সে দ্রুত পা চালিয়ে টং দোকানটা পার হয়ে গেল। অনেকটা দূরে এসে তাকিয়ে দেখল, লোকটা আর সেখানে নেই।
এসব কেন হচ্ছে? তানিমের মনে হলো, বিষয়টা মা–বাবার সঙ্গে আলাপ করা দরকার। যে লোকের মেঘালয়ে যাওয়ার কথা, সে তানিমের পিছু পিছু শ্রীমঙ্গলে নেমে গেল, মামার বাসা পর্যন্ত! আবার তার পিছু পিছু ঢাকায় চলে এসেছে! একবারে তার বাসার কাছে! কেন? কী চায় লোকটা? বাবাকে বিষয়টা বললে বাবা বলবেন, ‘আগেই বলেছিলাম, পাগলা ছটকুর ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। তোর মাথা খারাপ করে দেবে। এখন হলো তো?’ আর মাকে বললে মা সঙ্গে সঙ্গে তার ফুফাতো ভাই, যিনি পুলিশের বড় অফিসার; তাকে ফোন করা শুরু করবেন এবং উনিও নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে তানিমকে ডেকে পাঠাবেন তার অফিসে।
তার চেয়ে বরং বিষয়টা কিংশুকদার সঙ্গে আলাপ করা যাক। কিংশুকদা তাদের পাড়ার বড় ভাই, একটা কলেজের বিজ্ঞানশিক্ষক। তাঁর অনেক পড়াশোনা। সব বিষয়ে তিনি জানেন। পরদিন তাঁর কাছেই যাবে, এটা ভেবে মনটা শান্ত হলো তানিমের। অবশ্য কিংশুকদাকে তাঁর বাসায় পেলে হয়!
পরদিন সকালে নাশতা খেয়েই ছুটল তানিম। কিংশুকদার বাসা খুব দূরে নয়। একটা ছোট্ট একতলা বাসায় তিনি একাই থাকেন। ভাগ্য ভালো, কিংশুকদাকে পাওয়া গেল।
—কী রে, তুই হঠাৎ!
—কিংশুকদা, একটা জরুরি বিষয় নিয়ে এসেছি।
—তোর আবার জরুরি বিষয় কী রে? কোথাও যাসনি বেড়াতে? তোর বন্ধুরা তো মনে হয় কেউ নেই পাড়ায়।
—গিয়েছিলাম শ্রীমঙ্গলে। ওখানে গিয়েই বিরাট সমস্যায় পড়লাম।
—কী সমস্যা? চা খাবি?
—তুমি খেলে খাব।
কিংশুকদা চা বানাতে বানাতে বললেন, ‘শুরু কর তোর কাহিনি।’
তানিম একেবারে ট্রেনে কাটলেট খাওয়া থেকে শুরু করে সব খুলে বলল। বুড়ো লোকটার মেঘালয়ে না গিয়ে শ্রীমঙ্গলে নেমে যাওয়া, হঠাৎ ঘরের ভেতর ফ্রিজের সামনে দেখা পাওয়া, ঢাকায় ফেরার পথে গাড়ির চাকায় পলিথিন পেঁচিয়ে যাওয়া…তারপর ঢাকায় টং দোকানে দুই কাপ চা নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা; সব একে একে খুলে বলল তানিম। মাঝখানে কিংশুকদা কোনো প্রশ্ন করলেন না। তানিম থামলে পরে বললেন, ‘এক কাজ কর।’
—কী?
—পুরো ঘটনাটা তুই লিখে ফেল।
—লিখে কী হবে?
—দারুণ একটা ভৌতিক গল্প হবে। তারপর কোনো ছোটদের পত্রিকায় পাঠিয়ে দিবি।
—ঠাট্টা নয়! ব্যাপারটা কেন হচ্ছে কিংশুকদা?
—দাঁড়া, একটু ভাবতে দে। বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিতে হবে তো।
এ কথা বলে বারান্দায় চলে গেলেন কিংশুকদা।
কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, ‘আচ্ছা, তোর করোনা হয়েছিল না?’
—হ্যাঁ, দুবার। প্রথমবার তো আইসিইউতে থাকতে হয়েছিল তিন দিন। জান নিয়ে টানাটানি।
—হুম। আমার মনে হয় কি জানিস, করোনা যাদের হয়েছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকের কিছু না কিছু শারীরিক ক্ষতি হয়েছে। যেটা হয়তো এখন টের পাচ্ছি না, সময়মতো টের পাওয়া যাবে। তোর যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে স্মৃতিক্ষয়। তুই আবার সিরিয়াসলি নিস না, আমি আমার ধারণার কথা বলছি।
—তুমি ঠিক বলেছ। আজকাল অনেক কিছু আমি ভুলে যাই। মনে করতে পারি না।
—আমাকে শেষ করতে দে। মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক। খুব সম্ভবত তোর মস্তিষ্কের কিছু কিছু স্মৃতি মুছে গেছে করোনার সময়। মস্তিষ্ক যেহেতু শূন্যস্থান রাখে না, তাই সেই মুছে যাওয়া জায়গায় নতুন কিছু ঘটনা ঢুকে গেছে। এ ঘটনা কিন্তু তুই নিজেই তৈরি করেছিস। মস্তিষ্ক সুযোগ পেলেই শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলে, নতুন গল্প তৈরি করে। সুযোগটা তুই–ই করে দিয়েছিস। ঠিক তুই না, তোর অবচেতন মন। এই বুড়ো লোকের গল্পটা তোর শূন্যস্থান পূরণ করা গল্প। তোর মামার ফ্রিজের গল্পটাও এর সঙ্গে জুড়ে বসেছে। অনেকটা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বলতে পারিস।
—তার মানে তুমি বলতে চাইছ, বুড়ো লোকটা সত্যি নয়?
—হুম।
—আমার কল্পনা?
—হ্যাঁ তা–ই…
—অসম্ভব। লোকটা তো ট্রেনের ভেতর আমার সামনে এসে বসল, কথা বলল!
—তোর হয়তো তা–ই মনে হচ্ছিল। আসলে ব্যাপারটা সত্যি নয়। ব্যাপারটা অনেকটা জেগে স্বপ্ন দেখার মতো একটা ব্যাপার।
—মানে?
—যেমন ধর, প্লেন যখন মেঘের অনেক অনেক ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তখন পাইলটরা দেখেন শুধু নীল, নীল আর নীল আকাশ। তখন মস্তিষ্ক ভাবে, লোকটা মানে পাইলটটা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তাদের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। চিন্তা করে দেখ, একটা লোক দুই চোখ খোলা রেখে বসে আছেন, জেগে আছেন, কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন। অনেক পাইলট শুনেছি প্রথম প্রথম ভয়ও পান। পরে অভ্যস্ত হয়ে যান। রয়্যাল পাইলটদের ক্ষেত্রে এটা বেশি ঘটে; যাঁরা অনেক উঁচু দিয়ে রাজসিক প্লেন চালান।
—কিংশুকদা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কী করব?
—তুই এক কাজ কর।
—কী?
—এরপর ওই বুড়োর সঙ্গে দেখা হলে এড়িয়ে যাবি না। ভয় পাবি না। বরং এগিয়ে যাবি।
—তারপর?
—তারপর তার সঙ্গে একটা সেলফি তুলবি। পারবি না?
—পারব।
—ব্যস এটাই তোর সমস্যার সমাধান। ভালো কথা, আমি কিন্তু মনোবিজ্ঞানী নই বা মানসিক রোগের চিকিৎসকও নই। আমার মাথায় যে ব্যাখ্যা এসেছে, সেটাই তোকে বললাম, মানে শেয়ার করলাম আরকি! তুই বরং একজন ভালো মনোবিদকে দেখাতে পারিস। অধ্যাপক হেদায়েতকে দেখা। আমাদের দেশের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। উনি খুব সম্ভবত ধানমন্ডি ১৫ নম্বরে বসেন।
না, তানিম মনোবিজ্ঞানীর কাছে যায়নি। কারণ, ওই বুড়োকে আর দেখাও যাচ্ছে না। বুড়ো যেন পুরো গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটল। সেদিনও সে আরাফাতদের বাসা থেকে ফিরছিল। ওদের বাসা থেকে বের হতেই একটা শর্টকাট রাস্তা আছে। সেদিক দিয়েই আসছিল। রাস্তাটা একটা সরু চিপা গলির ভেতর দিয়ে গিয়ে আবার মূল রাস্তায় আসে। গলিটা খুব বড় নয়, দুই পাশে উঁচু দেয়াল। হেঁটে আসছিল তানিম। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। দেখে, সামনের দেয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে বুড়োটা। বাচ্চাদের মতো পা দোলাচ্ছে। মুখটা হাসি হাসি। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল তানিম। সেই ‘ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট’ অবস্থা! তখনই মনে পড়ল কিংশুকদার কথা। একটা সেলফি তুলতে হবে বুড়োটার সঙ্গে। সে কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে ফোনটা বের করল। বলল, ‘আপনার সঙ্গে একটা ছবি তুলতে চাই।’
বুড়োটা পা দোলানো বন্ধ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মুখে আগের সেই হাসি নেই। কাঁপা হাতে টপাটপ কয়েকটা সেলফি তুলল তানিম। তারপর খুব ধীরে হেঁটে বের হয়ে গেল গলিটা থেকে। একবারও পেছনের দিকে তাকাল না।
বাসায় এসে ছবিগুলো পরীক্ষা করল। একটাতেও বুড়োটা নেই। পেছনে শুধু উঁচু দেয়াল, দেয়ালের ওপাশে নীল আকাশ। তাহলে কি কিংশুকদার কথাই ঠিক? সবই তানিমের কল্পনা? বুড়োটা তার মস্তিষ্কের হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল…ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক হিসেবে? কে জানে!
এরপর ওই বুড়োকে আর কোথাও কখনো দেখেনি তানিম। বিষয়টা নিয়ে সে আর ভাবতেও চায় না।



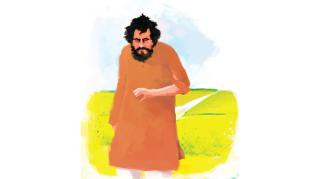 দাদার বড় ভাই। ভদ্রলোক কলকাতায় থাকতেন। দৈনিক আজাদ পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন, আর করতেন শিল্পচর্চা। তবে নির্দিষ্ট কোনো শিল্পে আবদ্ধ ছিলেন না। দৈনিক সওগাত পত্রিকায় তাঁর কিছু গল্প ছাপা হয়। শোনা যায়, সেগুলো পড়ে কবি নজরুল তাঁকে ডেকে প্রশংসা করেছিলেন। কলকাতা মিউজিয়ামে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছে একবার। আর যা করতেন, দাদাকে বড় বড় চিঠি লিখতেন। কয়েকটা চিঠি বাবার ড্রয়ারে আছে। ড্রয়ার পরিষ্কার করতে গিয়ে একদিন বাবার হাতে চিঠিগুলো ঠেকে এবং তাঁর অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। আমি সবগুলো চিঠি পড়েছি। সাধারণ গতানুগতিক কথার মধ্যে হঠাৎই এক-দুটো অদ্ভুত কথা লিখে বসতেন লোকটা। যেমন এক জায়গায় লিখেছেন: ‘বৌমার শরীর এখন কেমন? উহার যত্ন লইও। এখন উহার বিশেষ রূপ যত্ন আবশ্যক। প্রয়োজনে একজন সেবিকা নিযুক্ত করো। অর্থ লইয়া ভাবিত হইও না। কিছু পাঠাইলাম, প্রয়োজন সাপেক্ষে আরও পাঠাইব। অর্থ আমার কোনো কাজে আসে না।’ এরপরেই লিখলেন: ‘পৃথিবীটা সুবৃহৎ একখানা সময়যন্ত্র বিশেষ। আমি সূক্ষ্মতম কাঁটাটির উপর দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছি। এই ঘড়ি অসংখ্য কাঁটা সম্বলিত। সেকেন্ড, মিনিট আর ঘণ্টা বহির্ভূত অন্য কাঁটাগুলি সনাক্ত করিতে পারিতেছি না। অথচ সেকেন্ডের কাঁটায় উপনীত হইয়া আহ্নিক গতির মতো অচেনা কাঁটাগুলি অতিক্রম করিতেছি। ত্রাসে কম্পমান। আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকা অত্র সমাজের মানুষেরা এই কাঁটাগুলি দেখিতে পায় কি না জানি না, তাহাদের কোনো ভাবান্তরও পর্যবেক্ষিত হয় না। তোমার একজন বংশধর দরকার। আমি চাই আমার উত্তরাধিকারী। তুমি বংশধর পাইবে, সে ভবিষ্যতে বংশরক্ষা করিবে। কিন্তু উত্তরাধিকারী কবে আবির্ভূত হইবে? তবে সে আসিবে। আমি হয়তো তখন অস্তিত্বহীন। জানিব ও না যে সে আসিয়াছে। তবু আসিবে। একজনের জন্মের প্রতীক্ষায় বহু প্রজন্মকে জন্ম লইতে এবং দিতে হইবে। সে আসিবে। এই বহুকণ্টক ঘড়ির কাঁটাগুলিকে সে সনাক্ত করিবে অথবা ঊহ্য করিয়া দিবে, যাহা আমি পারিতেছি না। হয়তো জীবদ্দশায় পারিবও না। তবে অনুসন্ধান জারি থাকিবে।’
দাদার বড় ভাই। ভদ্রলোক কলকাতায় থাকতেন। দৈনিক আজাদ পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন, আর করতেন শিল্পচর্চা। তবে নির্দিষ্ট কোনো শিল্পে আবদ্ধ ছিলেন না। দৈনিক সওগাত পত্রিকায় তাঁর কিছু গল্প ছাপা হয়। শোনা যায়, সেগুলো পড়ে কবি নজরুল তাঁকে ডেকে প্রশংসা করেছিলেন। কলকাতা মিউজিয়ামে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছে একবার। আর যা করতেন, দাদাকে বড় বড় চিঠি লিখতেন। কয়েকটা চিঠি বাবার ড্রয়ারে আছে। ড্রয়ার পরিষ্কার করতে গিয়ে একদিন বাবার হাতে চিঠিগুলো ঠেকে এবং তাঁর অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। আমি সবগুলো চিঠি পড়েছি। সাধারণ গতানুগতিক কথার মধ্যে হঠাৎই এক-দুটো অদ্ভুত কথা লিখে বসতেন লোকটা। যেমন এক জায়গায় লিখেছেন: ‘বৌমার শরীর এখন কেমন? উহার যত্ন লইও। এখন উহার বিশেষ রূপ যত্ন আবশ্যক। প্রয়োজনে একজন সেবিকা নিযুক্ত করো। অর্থ লইয়া ভাবিত হইও না। কিছু পাঠাইলাম, প্রয়োজন সাপেক্ষে আরও পাঠাইব। অর্থ আমার কোনো কাজে আসে না।’ এরপরেই লিখলেন: ‘পৃথিবীটা সুবৃহৎ একখানা সময়যন্ত্র বিশেষ। আমি সূক্ষ্মতম কাঁটাটির উপর দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছি। এই ঘড়ি অসংখ্য কাঁটা সম্বলিত। সেকেন্ড, মিনিট আর ঘণ্টা বহির্ভূত অন্য কাঁটাগুলি সনাক্ত করিতে পারিতেছি না। অথচ সেকেন্ডের কাঁটায় উপনীত হইয়া আহ্নিক গতির মতো অচেনা কাঁটাগুলি অতিক্রম করিতেছি। ত্রাসে কম্পমান। আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকা অত্র সমাজের মানুষেরা এই কাঁটাগুলি দেখিতে পায় কি না জানি না, তাহাদের কোনো ভাবান্তরও পর্যবেক্ষিত হয় না। তোমার একজন বংশধর দরকার। আমি চাই আমার উত্তরাধিকারী। তুমি বংশধর পাইবে, সে ভবিষ্যতে বংশরক্ষা করিবে। কিন্তু উত্তরাধিকারী কবে আবির্ভূত হইবে? তবে সে আসিবে। আমি হয়তো তখন অস্তিত্বহীন। জানিব ও না যে সে আসিয়াছে। তবু আসিবে। একজনের জন্মের প্রতীক্ষায় বহু প্রজন্মকে জন্ম লইতে এবং দিতে হইবে। সে আসিবে। এই বহুকণ্টক ঘড়ির কাঁটাগুলিকে সে সনাক্ত করিবে অথবা ঊহ্য করিয়া দিবে, যাহা আমি পারিতেছি না। হয়তো জীবদ্দশায় পারিবও না। তবে অনুসন্ধান জারি থাকিবে।’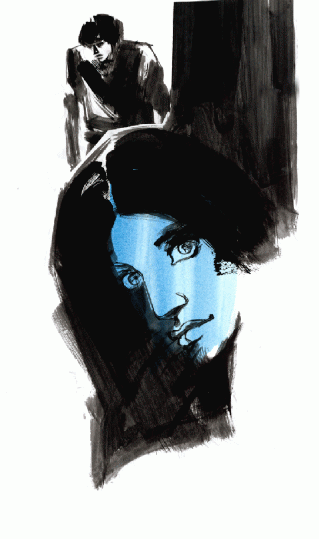 পাখিরা কীভাবে জুটি বাঁধে, তাই নিয়ে ভীষণ তর্ক লেগে গেল ওদের। ওরা তো দল বেঁধে থাকে, একসঙ্গে অনেক পাখি ঝাঁক বেঁধে ওড়ে, নামে, আবার সেভাবেই উড়ে যেতে থাকে। কিন্তু এর মাঝে কীভাবে দুজন করে আলাদা হয়ে যায়, খাবার খুঁটে খায়, নীড় বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চাও ফোটায় দুজন মিলেই। কীভাবে তারা নির্দিষ্ট একজনকেই বেছে নেয়, আবার দল বেঁধে উড়েও সেই জোড়া কি একই থাকে? কীভাবে থাকে? কেন থাকে?
পাখিরা কীভাবে জুটি বাঁধে, তাই নিয়ে ভীষণ তর্ক লেগে গেল ওদের। ওরা তো দল বেঁধে থাকে, একসঙ্গে অনেক পাখি ঝাঁক বেঁধে ওড়ে, নামে, আবার সেভাবেই উড়ে যেতে থাকে। কিন্তু এর মাঝে কীভাবে দুজন করে আলাদা হয়ে যায়, খাবার খুঁটে খায়, নীড় বাঁধে, ডিম পাড়ে, বাচ্চাও ফোটায় দুজন মিলেই। কীভাবে তারা নির্দিষ্ট একজনকেই বেছে নেয়, আবার দল বেঁধে উড়েও সেই জোড়া কি একই থাকে? কীভাবে থাকে? কেন থাকে?